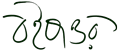
শিল্প আর দৈনন্দিনের জীবন : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
আমাদের দেশের বর্তমান শিল্প-আন্দোলন এখনও আমাদের বিপুল জনগণের মনের ভিতর প্রবেশ করতে পারেনি। জনজীবনে আমাদের শিল্প-সক্রিয়তার প্রভাব নানা কারণে সামান্য, যদিও সন্দেহ নেই যে আমাদের রুচির বৌদ্ধিক দিককে তা উদ্দীপিত করেছে। তবু, আমাদের দেশের মানুষ পঞ্চাশ বছর আগেও তাদের চারপাশ সম্পর্কে এত নিরুত্তাপ ছিল না। শিল্পকলার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাপনের সম্পর্ক ছিল অনেক স্বাভাবিক। সব সময়ে তাদের সমস্ত প্রয়োজন, আবশ্যকীয়তা বা বিলাস-ব্যসনের জন্য লোকে কারিগরদের তৈরি বিবিধ সম্পদের দিকে ঝুঁকেছে। এই কারিগররা, যারা নানান সুন্দর জিনিশ তৈরি করে, তারা যে এ ভাবে শুধু তাদের ব্যক্তিপ্রতিভাই প্রকাশ করে তা নয়, সেই সঙ্গে সময় ও জায়গাবিশেষে তদঞ্চলের অধিবাসীদের রুচিরও প্রতিফলন ঘটায়। হায়, সে সবই এখন ক্রমে পরিণত হচ্ছে ‘কিউরিও’তে।
আমাদের দেশে এমন অসংখ্য শিল্পনমুনা আছে যাতে আমাদের শিল্পীদের দক্ষতার সাক্ষ্য রয়েছে। যদিও এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা ব্যক্তি-শিল্পীর অবদান নিয়ে ভাবছি না, বরং ভাবছি জনজীবন নিয়ে, অন্তত সুন্দরের প্রতি প্রকৃত আকাঙক্ষা সেখানে যত দূর প্রকাশিত হয়েছে। এ দিক থেকে গ্রামজীবনের সামান্য আলোচনা যথেষ্ট উপযোগী ও আকর্ষণীয় হতে পারে, অন্তত সেখানে প্রাচীন সংস্কৃতি ও প্রথার যতটুকু আজও টিকে আছে। বাংলায়, এবং নিঃসন্দেহে ভারতের অন্যত্রও, গ্রামের বাড়ির চারপাশে আমরা আজও সৌন্দর্যের এই আকাঙক্ষা খুঁজে পেতে পারি। নিকট-অতীতেও যে-কোন সামান্য কাজে বা গ্রামের দৈনন্দিন কর্মে সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির একটা জায়গা ছিল। এমনকী নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষণস্থায়ী জিনিশও যত্ন ও রুচির সঙ্গে অলঙ্কৃত হত। রঙিন সুতোয় অলঙ্কৃত ‘কাঁথা’ যেমন আজ সরল সৌন্দর্য ও নকশার কারণে বিখ্যাত। এই কাঁথা একদা সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিশ ছিল, বিছানার চাদর বা গায়ের চাদর হিশেবে তা ব্যবহৃত হত। তারপর আছে ‘শিকা’ (দড়ি দিয়ে তৈরি ঝোলানো তাক, অবাঞ্ছিত চতুষপদ প্রাণীদের নাগালের বাইরে জিনিশপত্র রাখার জন্য ব্যবহৃত)— ভারি উপযোগী জিনিশ আর এত সুন্দর যে শুধু গৃহসজ্জার জন্যই তা ব্যবহার করা যায়। এ রকম আরও বহু জিনিশের কথাই বলা যায়, বাসনপত্র বা মিষ্টির ছাঁচ ইত্যাদি— সুন্দর সব জিনিশ, এখন তার জায়গা কেড়ে নিয়েছে শস্তা, আমদানি করা, কারখানার তৈরি মাল। বিভিন্ন জিনিশের ওপর বিভিন্ন রকমের ছবি, কাগজের স্টেনসিল ইত্যাদি ছিল গৃহবধূদের কাছে এক ধরনের বিনোদন আর নৈপুণ্যেরও বিষয়।
কিন্তু সাধারণ লোকের সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শনের সবচেয়ে বড় সুযোগ মিলত বিয়ের উৎসব, ব্রতপালন বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময়ে। এই সমস্ত অনুষ্ঠান, তার ধর্মীয় অর্থ যা-ই হোক না কেন, যারা এতে অংশ নিত তাদের নান্দনিক শিক্ষায় খুব বড় ভূমিকা পালন করত। আলপনা, ঘর সাজানোর সবচেয়ে সুন্দর উপায়, উদ্ভাবিত হয়েছিল এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সূত্রেই, এবং সম্ভবত বাংলার পট-ও তা-ই। ব্রত-অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পযন্ত পুরো প্রক্রিয়াটাই শিক্ষার। একই ভাবে, বিয়ের অনুষ্ঠানও, তার বিস্মৃত সামাজিক প্রথা ও বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত শিল্পনৈপুণ্য অনুশীলন করার যথেষ্ট সুযোগ দেয়। দক্ষ হাত এ অনুষ্ঠানে ব্যবহারযোগ্য প্রায় সব জিনিশই সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যদিও এর অধিকাংশ জিনিশেরই কোন স্থায়ী মূল্য নেই, তবু উপযোগিতা ও বাণিজ্যিক মূল্যের এই অভাবও উপচে-পড়া নান্দনিক আনন্দ থেকে তাদের নিরুৎসাহিত করে না।
এখানে আমি তেমন মাত্র কয়েকটা জিনিশেরই উল্লেখ করতে পারি, গ্রামের যে-কোন বাড়িতে যা সচরাচর দেখা যায় এবং যা তারই নিজস্ব। এর অধিকাংশই সাধারণ শিল্পীদের কাজ, মজুরি-নেয়া পেশাদারদের নয়। জিনিশগুলো তৈরিও সহজপ্রাপ্য উপাদানে, যেমন ব্যবহৃত বা ছেঁড়া কাপড়, দড়ি, বেত, ঘাস, নারকেল, ঝিনুক ইত্যাদি। এর জন্য খরচও সামান্য। এই সমস্ত জিনিশ, একদা আমাদের জনজীবনে কত বড় অংশই না ছিল এবং জীবনকে তা রঙে, চরিত্রে, লাবণ্যে ভরিয়ে তুলত। আর আজ, হায়, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে গবেষণার বিষয়। আজও সম্পূর্ণ বিলোপের হাত থেকে এই সমস্ত শিল্পকে বোধ হয় বাঁচানো অসম্ভব নয়।
এই সমস্ত অখ্যাত শিল্পকর্মে প্রকৃত আগ্রহের পথে যে-সমস্ত বাধা প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার একটা বোধ হয় এই যে, অর্থ-নিরপেক্ষ ভাবে শৈল্পিক মূল্যের কথা আমরা ভাবতে পারি না। এ সমস্ত শিল্পকাজের নমুনা যথাস্থানে দেখলে আমরা অবজ্ঞা করি এবং মিউজিয়মে কাঁচের বাক্সে অদ্ভত বলে যত ক্ষণ না আমাদের অভিজাত দৃষ্টির সামনে তা তুলে ধরা হয়, তত ক্ষণ খেয়ালও করি না। এবং তখনও আমরা শ্রদ্ধার ভাণ করি, প্রকৃত আনন্দ পাই না।
এই সমস্ত আলঙ্কারিক ঘরোয়া শিল্পের এক আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত হল আলপনা, সচেতন ভাবে যা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই বাংলার লোকে তাদের সংস্কৃতি ও নান্দনিক ঐতিহ্যের প্রতি বৌদ্ধিক আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। আলপনার ওপর অবনীন্দ্রনাথের মূল্যবান বইটিই এ ক্ষেত্রে প্রথম এবং এ বিষয়ে সাধারণজনের বর্তমান আগ্রহের পেছনে তার অবদান আছে। এ বইয়ে আলপনার বিভিন্ন নমুনার মূল্যবান সংগ্রহ আছে। দুর্ভাগ্যবশত, কার্পেট আর ভারি আসবাবে সংকীর্ণ আমাদের আধুনিক শহুরে বাড়িতে আলপনার ব্যবহারিক উপযোগের সুযোগ সীমিত। একে বাঁচানোর জন্য নিছক বৌদ্ধিক আগ্রহই যথেষ্ট নয়। সৌভাগ্যের কথা যে, শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা এ নিয়ে ভেবেছেন ও আশ্রমজীবনের অংশস্বরূপ বহু উৎসব-অনুষ্ঠানে তা ব্যবহার করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই, সচেতন শিল্পীদের হাতে এই প্রাচীন শৈলীর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।
এ ক্ষেত্রে একটা সতর্কবার্তা জরুরি। মৃতপ্রায় গ্রামীণ শিল্পের পক্ষে সওয়ালের সময়ে বা তার পুনরুদ্ধার ও পুনর্ব্যবহারের চেষ্টায় আমরা যেন আমাদের আধুনিক জীবনে গ্রামীণ শিল্পকে বিশুদ্ধ রাখার অবাস্তব কল্পনার পথে না-যাই। এ হল জাতীয় আবেগবাদীদের পথ, অসংলগ্ন কৃত্রিমতার দিকে টানতে গিয়ে আসলে এ ভাবে তারা শিল্পকে হত্যাই করে। এই অপ্রিয় সত্য আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে ভালো জিনিশেরও স্বাভাবিক মৃত্যু সম্ভব। বাঁচতে হলে শিল্পেরও প্রয়োজনীয় সামাজিক শর্ত পূরণ করতে হবে। পৃষ্ঠপোষকদের নিছক অভিপ্রায়ে তা বাঁচতে পারে না। যদি সামগ্রিক ভাবে আমাদের জীবন হয়ে গিয়ে থাকে বা হয়ে পড়তে থাকে আরও জটিল, আরও বৌদ্ধিক, তবে আমাদের শিল্পেও তার ছাপ আমরা এড়াতে পারি না। আদর্শটা হল আমাদের প্রথার, ঐতিহ্যের সেরা অংশটা গ্রহণ করতে হবে, মিশরী মমি-র তাকে সংরক্ষিত করে কোন লাভ নেই।
দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীণ শিল্প বা পুনর্নবায়িত আলপনার শিল্প কত দিন চলবে, আজকের জীবনযাপনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার ওপরই তা নির্ভর করছে। এই পুনরুদ্ধারের প্রভাবে হতে পারে যে আধুনিক আলঙ্কারিক শিল্পেরও যথেষ্ট ভালো হবে। অন্তত এই অর্থে এবং এই পযন্ত ঐতিহ্যগত শিল্পের আলোচনা আমাদের শিল্পীদের পক্ষে মূল্যবান।
‘আর্ট অ্যান্ড ডেইলি লাইফ’ নামে এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘দ্য বিশ্বভারতী কোয়ার্টর্লি’র মে-জুলাই ১৯৩৯ সংখ্যায়। পরে অন্তর্ভুক্ত হয় বিনোদবিহারীর শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক রচনা সংকলন ‘চিত্রকথা’য় (অরুণা প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৮৪)। এখানে রইল তার বাংলা অনুবাদ, করেছেন সন্দীপন ভট্টাচার্য।
(এখানে প্রকাশিত লেখাপত্র শুধুই পড়ার জন্য। দয়া করে এর কোন অংশ কোথাও পুনর্মুদ্রণ করবেন না। ইচ্ছে করলে লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন, কিন্তু অনুরোধ, গোটা লেখাটি কখনওই অন্য কোন ওয়েবসাইটে বা কোন সোশ্যাল নেটওয়রকিং সাইটে শেয়ার করবেন না। ধন্যবাদ।)